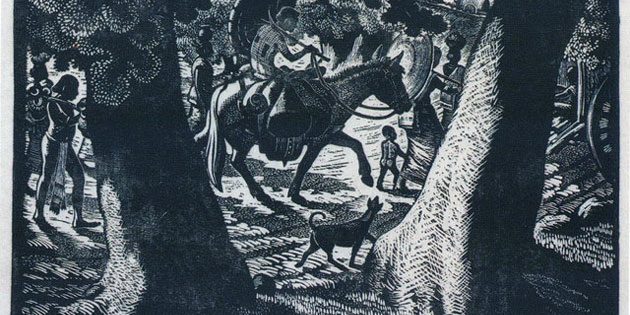অনেকদিন আগে, সম্ভবত আমার কৈশোরের জীবন জুড়ে থাকা বাগানের কোনো এক গাছের নিচে আমি একটি ছায়া দেখেছিলাম। বিমূর্ত মানবীর ছায়া। আমি শহরে বড়ো হওয়া ছেলে, তাও খোদ রাজধানী। আমার কাছে কৈশোর মানে স্কুল ছুটির পর আম্মার জন্যে মাঠের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা, দুরন্তপনা মানে সহপাঠী বন্ধুর সাদা শার্টে কলম দিয়ে আঁচড় কাটা, আমার বিষণ্ন চোরাগলির শহুরে জীবনে আকাশ মানে জানালা দিয়ে যেটুকু নীল দেখা যায়, সেটুকু।
আমার শৈশব বলে কিছু নেই; ‘ভালো স্কুলে ভর্তি হবার’ চাপে আমার শৈশব নিহত হয়েছে আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই। এবং আমার কৈশোর পালিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, আমাকে নিঃস্ব করে দিয়ে আমার কৈশোর পাখি হয়ে গেছে।
তবুও কৈশোরের জীবন জুড়ে থাকা বাগানের কোনো এক গাছের নিচে দেখা সেই বিমুর্ত নারীর ছায়া আমাকে বহুকাল জাগিয়ে রেখেছিলো। আমার মৃত্তিকা-সংলগ্ন ক্লেশগুলো সে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো— যেমন পলিমাটি ভাসিয়ে নেয় মিহিন বৃষ্টি; আবার যখন আমি ঘুমোতে পারতাম না, ক্রমাগত নুব্জ্য হতে থাকতাম আমার এবং আমার পূর্ব-পুরুষদের শতাব্দী পেরোনো ক্লান্তিগুলোর ভারে— তখন সেই বিমূর্ত মানবীর ছায়া আমাকে ঘুম পাড়িয়ে যেতো, আমি ঘুমাতাম, যেমন ঘুমিয়েছেন আমার প্রপিতামহ। সেই বিমূর্ত নারীমূর্তির কোনো নাম নেই। শুধু আমি ছাড়া আর সবার কাছে সে কখনো বিকলপক্ষ অতীত, কখনো হারিয়ে যাওয়া অনুপ্রেরণা, কখনো মহাকাব্যের মহাসময়। কেবল আমার কাছে সে নামহীন এবং তারপরেও তার একটি অপূর্ব নাম আমি দেই; লাজুক শাপলার ঠোঁটের কোণে জমে থাকা হাসির মতো আমি তাকে ‘একাত্তর’ নামে ডাকি।
অক্টরলনি মনুমেন্ট এবং তেরঙা ঝাণ্ডা
আমার শিরার ভেতরে প্রায়শই একটা অগ্নিপাখি উড়ে যায়, আমি টের পাই। পাখিটা চায়— আমি বিদ্রোহী হয়ে উঠি; সে আমাকে বারবার বলে— ইতিহাস পড়ো, জানো কে ছিলেন তোমার পূর্ব-পুরুষ। আমি ইতিহাস পড়ি না, ক্যালেন্ডার জুড়ে আছে অমর্ত্য সেনের ছবি, ক্যালেন্ডার ঝুলছে দরিদ্র নুরুমিয়ার ছাপড়া ঘরে। অমর্ত্য সেন হাসছেন, হাসছে অর্থনীতি; নুরুমিয়ার ক্যালরি হিশেব করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা; এক ওবামা প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে থাকে আড়াইশ কোটি মানুষ। পাশ্চাত্যের কার্নিশ বেয়ে পড়ে বিলাসী জল, ওদিকে তৃতীয় বিশ্বের কেবল কাপড় খোলা বাকি। এসব হর-হামেশাই ঘটছে; এবং ঘটবে। আমি নস্টালজিয়ার চৌকাঠে বসে পিঠ চুলকাই। পাশের বাসার ফুটফুটে শিশুটাকে দেখে কষ্ট পাই না, যদিও জানি এক অস্থির ভাগাড়ে তার জন্ম, যদিও জানি জন্ম-মাত্রেই সে ঋণগ্রস্থ।
এসব কোনো কিছুই আমায় আলোড়িত করে না; আমি বরং অধিকতর নষ্ট হই, যেমন নষ্ট ছিলাম একদিন। অথচ অগ্নিপাখি আমায় নিয়ে যায় অক্টরলনি মনুমেন্টে। সেই ১৮৩০ সালে, ফ্রান্সে তখন রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয়ে জুলাই বিপ্লব শুরু হয়েছে। কোলকাতার অক্টরলনি মনুমেন্টে গভীর রাতে কারা যেনো অপসারণ করে ইংরেজদের জয় পতাকাটি আর সেখানে উড়িয়ে দেয় ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার তেরঙা ঝাণ্ডা।
সেদিনের এই ঘটনাটি বঙ্গদেশের (বর্তমান বাঙলাদেশ ও পশ্চিমবাঙলার) সমগ্র জনসমাজ কিংবা ছাত্রসমাজের মধ্যে কেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো, আমি জানি না— তবে এটুকু জানি, সেদিন, সেই সূর্যমুখী সময়েই জন্ম নেয় ‘একাত্তর’।
‘পার্থেনন’— তোমার মাস্টহেড জুড়ে শূন্যতা
একজন চলে যান। না, মৃত্যু বলে কোনো কিছুকে কোনোদিন আমরা স্বীকার করিনি। আমরা জানি, মৃত্যু এক ভাওতাবাজী, প্রতারণা। আসলে মৃত্যু হয় না কোনোকিছুর, সবকিছু বেঁচে থাকে, কেবল প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় প্রকৃতির কিংবা নেমেসিসের প্রকৃতি সইতে পারে না সত্তাকে। ডিরোজিও তাই আছেন, হয়তো তাঁকে ধারণ করবার মতো সাহস নেই প্রকৃতির, কারণ এখন প্রকৃতি বড়ো বিপন্ন এবং ছোটোলোকেরা প্রকৃতির সেবাদাস। প্রকৃতি এখন বাতিল বিউগল।
প্রকৃতি যখন ডিরোজিওকে সইতে পারলো না, ইতিহাস তখন প্রচার করলো ‘ডিরোজিও মৃত’। ইতিহাসও মিথ্যে কথা বলে— আমি আবারও বলছি, এবং বিশ্বাস করেই বলছি, ইতিহাসও মিথ্যে কথা বলে। ডিরোজিওকে না পেয়ে তাঁর শিক্ষার্থীরা তাঁর বিদ্রোহের বাণী সারাদেশে প্রচার শুরু করে। ইয়ং বেঙ্গল ছাত্রকর্মীরা ‘পার্থেনন’ নামে একটি সংবাদপত্রও বের করার চেষ্টা করে। একটিমাত্র সংখ্যা বের করার পরেই রক্ষণশীল সমাজপতি ও ইংরেজ সরকার তা বেআইনি ঘোষণা করে। সেটাই ছিলো ছাত্র সমাজের উদ্যোগে বের হওয়া প্রথম বাঙলা সংবাদপত্র।
আফিমের নেশা, মহাসঙ্কটের কাল
আগেই বলেছি— আজ আপনাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করেই লিখছি। আজ লিখছি, কেবল আমার প্রিয়তমা ‘একাত্তর’ এর জন্যে। আজ আমাদের কথা লিখছি। জুডাস কোনোদিন প্রেম করেনি, করলে সে বিশ্বাসঘাতক হতে পারতো না। সেনাবাহিনীকে হাজার চেষ্টা করেও প্রেমিক বানাতে পারেননি শহীদ কাদরী, কারণ প্রেমিক হলে সেনা-সদস্য, সেনাকর্তা হওয়া যায় না।
১৯০৭ সাল থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি কাঠামোগত ইতিহাস পাওয়া যায়। সেই থেকে সংগঠিত বিভিন্ন দাঙ্গার অধ্যায় বিবেচনা করলে দেখা যায়— ময়মনসিংহ, জামালপুর, কুমিল্লায় বা এতদ-অঞ্চলে সংগঠিত দাঙ্গাগুলোর প্রায় অভিন্ন চরিত্র। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান ফারাককে মুখ্য করে পরস্পরের অভিন্ন স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে গোষ্ঠীচিন্তা উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়, বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করে হিংসা ছড়ানো হয় এবং পরিণামে এই হিংসা রক্তাক্ত সংঘাতের রূপ নেয়। এই হিংসা ছড়ানো তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় ময়মনসিংহের জনৈক ইবরাহীম খাঁ প্রণীত লাল ইশতেহার নামক চরম সাম্প্রদায়িক প্রচার পুস্তিকায়। এর ভাষা ও বক্তব্য এতোই নিম্নরুচির ও উস্কানিমূলক ছিলো যে ঢাকা সম্মেলন ও ১৯০৭ সালের মার্চে বরিশালে অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে কয়েকজন মুসলিম নেতা এর প্রচারণা ঠেকাতে উদ্যোগী হযেছিলেন।
এরপর আরও রাজনীতি হয়েছে। দেশভাগ হয়েছে। ভাগ হয়েছে মানচিত্র; কারা যেনো হিন্দু, কারা যেনো মুসলমান— অথচ কেউই মানুষ বিবেচিত হয়নি সেদিন, সহপাঠী বন্ধু হয়ে গেছে অন্য দেশের নাগরিক, অন্য কেউ, সে আর আমার থাকে না। দ্বি-জাতিতত্ত্বের মতো ভাওতাবাজীর দর্শনে ভাগ হয় সব, ভাগ হয় সংস্কৃতি— কেবল হৃদয় ভাগ হয় না, বৃষ্টি ভাগ হয় না, রোদ ভাগ হয় না। তাই হৃদয় এখনো কাঁদে, এখনও বৃষ্টি ঝরে ‘দুই বাঙলা’য় সমানভাবে, একই রোদে বেনী দুলিয়ে স্কুলে যায় দুই বাঙলার কিশোরীরা।
দেশভাগ কেড়ে নেয় সত্যেন বোসকে; মিহির দাশগুপ্তের মতো অনন্য ছোটোগল্পকার পাড়ি জমান কোলকাতায়, বেদনায় আর লেখেননি তিনি, চুয়াল্লিশে শেষ লিখেছিলেন সন্ধ্যা বেলার গান। পদ্মা’র তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ঋত্বিক ঘটক কেবলই কেঁদেছিলেন, ফিরে আসতে পারেননি।
এরপর ‘পান–বিড়ির পাকিস্তান’ আর মুসলমানের গোলায় ‘ধর্মীয় ধান’
তৈরি হয় পাকিস্তান। কোনো রাষ্ট্র হিসেবে নয়; জিন্নাহর বেঈমানির তীর্থকেন্দ্র হিশেবে। সাতচল্লিশের ১৪ই আগস্ট থেকে আটচল্লিশের একুশে মার্চ— মাঝখানে সময় সাতমাস সাতদিন। জিন্নাহর চরিত্র ধরা পড়ে, জিন্নাহ রেসকোর্সে উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়। তখনও মুসলমান বাঙালি তার মুসলমানিত্ব রক্ষার স্বপ্নে বিভোর। কেবল সংস্কৃতমনা মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়— ফলশ্রুতিতে রচিত হয় বায়ান্নর আখ্যান এবং ছাপ্পান্নতে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়- ‘প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা’।
আগেই বলেছি— পাকিস্তান একটি বেঈমান রাষ্ট্র এবং চাঁন-তারা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত পতাকা। বেঈমান জাতি তাদের স্বরূপে প্রতিভাস হয়। বাঙালিকে ক্রমেই নিয়ে যেতে থাকে অপমান-অবহেলার চূড়ান্ত দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু বাঙালির রক্তস্রোতে যেহেতু সংগ্রামের অগ্নিশপথ— বাঙালি উজ্জীবিত হয়, প্রতিরোধ করে এবং বাঙালির আকাশে এক নক্ষত্র জ্বলে উঠেন। লাল-সবুজের পতাকা উত্তোলিতো হয় মুক্তাঞ্চলে— কেবলই মুক্তাঞ্চল, কেবলই মুক্তাঞ্চল; ধ্বনিত হয় জয় বাঙলা, স্বাধীনতা লাভ করে বাঙলাদেশ; ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের প্রাণময় শরীরে নেমে আসে একাত্তরের বৃষ্টি।
উননিশ শো একাত্তর- আগামী এক হাজার শতাব্দী পরেও বাঙালির অখণ্ড অনুপ্রেরণার নাম।
মধ্যরাতে নির্ঘুম কবি এবং স্মিতহাস্য রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার একটি ব্যক্তিগত অনুভূতি আছে। অন্য কোনো লেখায় হয়তো সেটি জানানো যাবে। একজন রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন জেগে ওঠেন, প্রতিদিন ঘুমোতে যান এবং তন্দ্রা-জাগরণে তিনি রবীন্দ্রনাথ হয়ে থাকেন, গীতবিতানের প্রশান্তিময় আন্দোলনের মতো— রবীন্দ্রনাথ সারারাত একলা জাগিয়ে রাখেন আমাকে। তারপরও বলছি— রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসি আমি, এবং রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসি না। কখনো রবীন্দ্রনাথকে আদরে বুকে জড়িয়ে ধরি, কখনো তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখি এবং কখনো রবীন্দ্রনাথের হাতে হাত রেখে দীর্ঘ-ব্যাপ্ত পথ পাড়ি দিই। অভিমান করি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, মাঝে মাঝে কেবল চতুরঙ্গ ছাড়া বাদবাকি উপন্যাসগুলোকে বাতিল করে দিই। আমাদের হরহামেশা বাতিল করে দেয়া রবীন্দ্রনাথ একদিন আরও আরও তীব্রভাবে প্রাসঙ্গিক হবেন পৃথিবীর কাছে। বাতিল হয়ে যাবো আমরা; কেবল মুহূর্ত সাজাবে ক্যানভাস নৃ-তাত্ত্বিক পুস্তকের ভাষায়।
কৈশোরের শেক্সপীয়র, যৌবনের শেক্সপীয়র
আমার কৈশোরটা একেবারেই মাঠে মারা যায়নি। প্রাণময় বিকশিত সত্তা একে একে ডানা মেলেছে চারধারে— সে সময় শেক্সপীয়রকে কেনো যেনো অনেক বড়ো মনে হতো, মনে হতো তিনি যেনো আল্লাহ— সৃষ্টি করছেন, ধ্বংস করছেন আবার ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কোনো বিরাম নেই তাঁর। হ্যামলেট পড়ে হ্যামলেট হবার স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিং লেয়ার কাঁদিয়েছেন দশম শ্রেণি পর্যন্ত— কী অসামান্য থরোথরো কৈশোর, তবুও অর্থহীন মনে হয় তাকে। আর এই যৌবনে এসে হঠাৎ শেক্সপীয়রের সনেটগুলোকে মনে হচ্ছে প্রাণ-সর্বস্ব আর নাটক— কেনো যেনো সেগুলো আর ভালো লাগে না, কেনো যেনো মনে হয়— কষ্ট করে বৃথাই আড়াইশ তিনশ লাইন কণ্ঠস্থ করা হয়েছিলো, কোনো দরকার ছিলো না।
তবুও একজন শেক্সপীয়র প্রতিমুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ- কেবল তাঁর সনেটগুলোর জন্যে।
সেইসব সাহিত্য— যেগুলো আমাদের, যেগুলো আমাদের নয়
কম্পটনের একটা গ্রন্থ পাওয়া যায়— ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস নামে। আমি বইটি লাইব্রেরি থেকে চুরি করেছিলাম। বই এবং হৃদয় চুরির মধ্যে আমি কোনো পাপ দেখি না। সেই বইটি পড়ে বুকের ভেতরে কষ্ট বাসা বাঁধে। তারপর কষ্ট চলে যায়। একজন ল্যায়ামনের ব্রুট পড়ে ব্রিটেনের ইতিহাস জানা যায়, আর তার সাথে সাথেই যখন পড়া হয় নীরোদ সি চৌধুরীর আত্মঘাতী বাঙালি তখন জীবনকে অর্থপূর্ণ মনে হয়। আবার বিভ্রান্ত কবি ইলিয়ট মাঝে মাঝেই বিনোদন হয়ে ওঠেন। তাঁর দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড যখন পড়া হয়, আর যদি জানা যায় ১৯২২ এ এটি প্রকাশিত, তবে হাসি চেপে রাখা দুস্কর হয়ে ওঠে। ইলিয়টকে ইডিয়ট মনে হয়েছে বহুবার এবং এখনও মনে হয়, তবে ভালোও লাগে— বিভ্রান্ত ও শিশুদের ভালোবাসতে খুব ভালো লাগে।
আবার একটু পেছনে ফিরে যাই। আর্তনাদ যুগের কবিদের কথা মনে করি, সাহিত্যের ভাষায় যাঁদের ‘ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েটস’ বলা হয়। সেই হার্বাট, মার্ভেল, ক্রোশো, জন মিল্টন এবং সে যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় জন ডান। এঁরা প্রত্যেকেই কবি ছিলেন এবং ছিলেন স্রষ্টা কিন্তু তাঁরা কেউই গভীর ছিলেন না।
এরপরে যাঁদের পাই— তাঁরা কেবলই তুলনার জন্যে। তাঁদের কিছু কিছু সৃষ্টি কেবলই স্পর্শ করে, আলোড়িত করে না। মার্গারেট ক্যাভেন্ডিস তাঁদের অন্যতম; কিন্তু ক্যারল আর ডাফির তুলনায় সবই ম্লান।
তবে এগুলো কেবলই ছুঁয়ে যাওয়া— কোনোটাই স্থায়ী ভালোবাসা নয়, কেবল প্রথম দেখা মাত্র।
বোদলেয়্যার, অ্যালেন পো ও আমার পঞ্চ পাণ্ডব
একেবারে ধরে কথা বললে— সাহিত্যের জগতে তুমুল বৃষ্টি নামান শার্ল বোদলেয়্যার। এলোমেলো করে দেন এবং নিয়ত ভাসান আমাকে। এঁরা কবি, এঁরা স্রষ্টা। আমি বিশ্বাস করি— সাহিত্য সবার জন্যে নয়, সবাই সাহিত্য পড়বে না— সবাই এমবিএ করবে, সবাই প্রকৌশলি কিংবা চিকিত্সক হবে, সবাই ব্যাবসা করবে, জীবিকা নির্বাহের তাগিদে প্রয়োজনে ‘এ ধার কা মাল ও ধার করবে’— কিন্তু সাহিত্য সবাই পড়বেন না। সাহিত্য সবার জন্যে নয়, এ কেবল তীব্র অনুভূতিপ্রবণ মানুষদের জন্যে। যেমন সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র সবার জন্যে, কিন্তু ঋত্বিক কিংবা বার্গম্যান সবার জন্য নয়। অতএব বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথকে বোঝার লোক পাওয়া গেছে, রবীন্দ্রনাথের মুরিদ জুটেছে, ধর্মের তকমা লাগিয়ে নজরুলের মতো একজন অসাধারণ কবি ও সঙ্গীত স্রষ্টাকে সাধারণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে; এবং দেখা গেছে বাঙালির সাহিত্য দৌড় ওই পর্যন্তই। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা বাঙালি পড়ে না, বিষ্ণু দে-কে বাঙালি ভয় পায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পড়ার যোগ্যতা অধিকাংশ বাঙালিই অর্জন করেননি; তবে সে তুলনায় জীবনানন্দ কিংবা বুদ্ধদেবের অবস্থা ভালো। টি-শার্টের কল্যানে আর অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের আধুনিক বাঙলা কবিদের কবিতার মাহাত্ম্যে বাঙালি তরুণ বুদ্ধদেব কিংবা জীবনানন্দের নাম শুনেছে এবং পড়ছেও। এটা আনন্দের।
‘অভিমানী ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা’ বা কাম্যু-সার্তে-কিয়ার্কগার্দ
আলবেয়্যার কাম্যু আমার চেতনার পাখি। কেবল আউটসাইডারের জন্যে নয়। কাম্যু প্রেরণা আরও অনেকগুলো কারণে, অনেকগুলো সত্য কথা নিখাদ নির্মোহ কণ্ঠস্বরে বলে দেবার জন্যে। আমাদের দুটো সমস্যার একটি হলো— অতীত ঐশ্বর্য ভুলে যাওয়া এবং অন্যটি হলো ‘অর্থহীন প্রলাপে’ অভিসন্দর্ভ লেখা। আজকাল গণমাধ্যম আর ফেসবুকের কারণে অভিসন্দর্ভ লিখতে হয় না— যখন যা মনে আসে— বলে দেয়া যায়। তেমনি ‘হতাশা’ একটি বিষয়। কারণে অকারণেই হতাশ হবার মতো বিবৃতি দেয়া হয়; এবং এটা জানার চেষ্টাও করা হয় না যে— ‘আশাহীনতা’ আর ‘হতাশা’ এক বিষয় নয়। কাম্যু আমাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, এবং উত্তরও দিয়েছিলেন— জানিয়েছিলেন, অস্তিত্ব হলো চূড়ান্ত আশাহীনতা। আশাহীনতা একটি দর্শন-কেন্দ্রীক প্রপঞ্চ, একে গড়পরতা ব্যবহারের রীতি সম্ভবত বাঙলাদেশের মানুষের মধ্যে প্রবল। এখানে স্বপ্ন দেখা যেমন সহজ, স্বপ্ন ভাঙাও সহজ। মিথ অব সিসিফাস — কখনোই অ্যাবসার্ডইজমকে ব্যাখ্যা করেনি, কারণ কাম্যু সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন অ্যাবাসার্ডইজমের চূড়ান্ত সত্তায় আত্মহত্যা নয়, বিদ্রোহ হতে পারে। সিসিফাসকে সুখী কল্পনা করার যে আত্মতৃপ্তিবোধে কাম্যু একশত সাঁইত্রিশ পাতার বইটি শেষ করেছিলেন, তার কতোটুকু সার্থক হয়েছে কিনা জানি না— তবে সিসিফাসকে সুখী মনে করি না আমি। আসলে সুখটাই অর্থহীন এবং বিমূর্ত— পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সুখী হবার, প্রেমিক হবার, দম্পতি হবার অভিনয় করে মাত্র।
ব্যক্তির অ্যাবসার্ডিটি নিয়ে সার্তে অনেক কথা বলেছেন এবং সুলেখনীতে তা প্রতিষ্ঠিতও করেছেন। কিন্তু শেষের দায়টি তিনি এড়াতে পারেননি, তিনি সৎ ছিলেন এবং সে কারণেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন স্কেচ অব থিওরি অব ইমোশন — যার জন্যে তিনি বেঁচে আছেন এবং থাকবেন। যদিও মৃত্যুকালে বা তার অদ্যাবধি আগে তিনি বলেছিলেন— নৌসিয়া ও নো এক্সিট এর জন্যে তিনি টিকে থাকবেন। নোবেল পুরস্কারের মতো ফালতু বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বলেছিলেন— তাঁকে পরিমাপ করার মতো কিছু নেই এই গ্রহে। সেই সার্তে বলতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত, যা পারেননি বলতে কাম্যু— অ্যাবসার্ডইজমের চূড়ান্ত রূপরেখার কথা।
আর কিয়ার্কেগার্দের প্রসঙ্গে কিছু বললাম না। তিনি শক্তিশালী ছিলেন। তাঁকে নিয়ে বলবার মতো মেধা বা পড়াশুনা যেদিন হবে— সেদিন তাঁকে নিয়ে লিখবো। তিনি বড়ো এবং মহৎ— এ দুটো বিশেষণ খুব কম মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
প্রাচ্যবোধি সামুয়েল বেকেট: এহো বাহ্য, আগে কহ আর
তিনি জন্ম নিয়েছিলেন আয়ারল্যান্ডে শতেক বছর আগে এবং বেঁচে আছেন আমার লাইব্রেরিতে। তাঁর সামগ্রিক জীবনপঞ্জি নিয়ে আলাদা আলোচনার প্রয়োজন নেই— বিদগ্ধমাত্রেই তাঁকে জানেন। তবুও তিনি দু পর্যায়ের জীবনযাপন করেছেন। ১৯০৬ থেকে ১৯৫৩ বা ’৫৫ পর্যন্ত। শেষ দু বছরেই তিনি প্রকাশ করেছেন পৃথিবী চমকে দেয়া নাটক ওয়েটিং ফর গোডো — এবং কাঁপিয়ে দিয়েছেন জীর্ণ বিশ্বকে। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর টালটমাল পৃথিবীতে লিখতে শুরু করেন; ১৯২৯ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত লিখেছেন দুটি প্রবন্ধ, কিছু কবিতা এবং একটি ছোটোগল্প সংকলন। মারফি উপন্যাসটি প্রকাশ করেছেন ১৯৩৮ সালে— সাহসী উপন্যাস, সে সময় এমনটি লিখতে পারেননি কেউ। তিনি দেখেছেন অ্যাবসার্ডিটির হাতে পুতুল, কোনো ঈশ্বর তিনি দেখেননি।
বার্কলে বেকেট এমন সময়ে লিখছেন— যখন বাইরের পৃথিবী ধ্বংসের শেষ কিনারে। মানুষের অস্তিত্ব অনিশ্চিতের আঁধারে অন্ধ পথিক। বেকেটের অন্তর্জগতে তখন উত্তাল জীবন জিজ্ঞাসা। তিনি নিজেকে খুঁজেছেন। এবং পাননি শেষ পর্যন্ত— এটাই নিয়তি। সেই নিয়তিতেই বাস আমাদের, এবং আমরা সেই ‘না পাওয়াটাকে’ই ধারণ করি, লালন করি।
সেই বোধই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে। ম্যঁলয়–ম্যালনডিয়্যাস–আননেইম্যাবল ত্রয়ী উপন্যাসে জীবন বাস্তবতার স্বরূপ এসেছে। যেখানে আমরা জীবিত হই, এবং মনে করি, আমরা মৃত ছিলাম একদিন। সহৃদয় ম্যঁলয় এবং হৃদয়হীন মোরান আমাদের চারপাশেই বা আমাদের ভেতরেই থাকে। ম্যঁলয় মায়ের নাম ভুলে যায়— কখনো সব ভুলে যায়; আর আমরা সব মনে রাখার ভান করি। ম্যালনডিয়্যাস এক মৃত্যুমুখী মানুষের স্মৃতিকথন। অন্য নামও দেয়া যায়— ম্যান অ্যালন ডাইস। দিন তার অনিশ্চিত— যেমন বেকেটেরও ছিলো। অসংলগ্ন স্মৃতিচারণ চলে মেলনের, কখনো মনে পড়ে ব্রিটিশবিরোধী আইরিশ নেতা ম্যাকসুইনের কথা। কখনো সে বলে কৃষক ল্যাঁবেয়ার কথা— এক মৃত্যুপথযাত্রীর চোখে দেখা জগৎ, আমরা প্রতিনিয়তই দেখছি, আমরা প্রত্যেকেই মৃত্যুপথযাত্রী— স্বীকার করুন আর না করুন। আনন্যামেবলের ম্যাকমেন ভবঘুরে। আমার ভীষণ প্রিয় চরিত্র। শহরে ঘুরতে ঘুরতে সে গ্রামে চলে যায়, জঙ্গলে চলে যায়— যেনো ‘ম্যঁলয়েরই পুনরাবৃত্তি’। এরপর সে নিজেকে আবিস্কার করে— মৃত্যুমুখীন সরলরেখাতে। সবকিছু শূন্যতায় শেষ হয়। শূন্যতার মাহাত্ম্য-বন্দনা যেনো।
একজন বঙ্গবন্ধু এবং সবকিছু অর্থহীন
খোঁজ লাগালে দেখা যাবে অধিকাংশ বাঙালি যাঁকে পছন্দ করেন— তিনি বঙ্গবন্ধু, এবং এটাও দেখা যাবে অধিকাংশ বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে প্রতিনিয়ত হত্যা করছেন; কারণে অকারণে বঙ্গবন্ধুকে ব্যবহার করছেন। বাঙলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি সাতকোটি জনতার ত্যাগের মহীরূহ, যে সাতকোটি জনতার মিলিত উপাখ্যানের নাম ‘বঙ্গবন্ধু’। বঙ্গবন্ধু কখনোই কোনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না, তিনি বাঙালির নেতা ছিলেন, তিনি ‘আমাদের লোক’- আমরা, যারা সকালে ঘুম থেকে উঠে পেটের তাগিদে রাস্তায় নামি, বঙ্গবন্ধু আমাদের নেতা; বঙ্গবন্ধু আমাদের ইতিহাস, আমরা যারা শ্রমে-সংগ্রামে প্রতিদিন বাঙলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি— বঙ্গবন্ধু আমাদের নেতা। বঙ্গবন্ধুর সাথে বাঙলাদেশ আওয়ামী লীগের কোনো সম্বন্ধ আছে কি নেই— তা জানার দায়িত্ব আমাদের নয়। বঙ্গবন্ধু এক কবি— যিনি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের জন্য প্রতিনিয়ত কবিতা লিখেছেন এবং লিখতে লিখতে একটি মহাকাব্য গড়ে তুলেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং জেনেছিলেন— বাঙালি তাঁকে ভালোবাসে। কিন্তু পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে একজন বঙ্গবন্ধুর বুকে আশ্রয় নিয়েছিলো বুলেট, রক্ত গড়িয়ে পড়েছিলো বাঙলার পলিমাটিতে। এতে আওয়ামী লীগের কী ক্ষতি হয়েছিলো জানি না, ক্ষতি হয়েছিলো বাঙলাদেশের, ক্ষতি হয়েছিলো বাঙালির— বাঙলার মানুষ বঞ্চিত হয়েছে একটি উন্নত রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ থেকে।
বঙ্গবন্ধুর সাথে ‘জয় বাঙলা’ও বাঙালির স্লোগান। কোনো রাজনৈতিক দলের স্লোগান এতোটা কাব্যমুখর হবার প্রয়োজন নেই, কেবল বাঙালির স্লোগানই হবে ‘জয় বাঙলা’। বাঙালি তাঁর আনন্দ-বেদনা, উত্সাহ-উত্সবে উচ্চারণ করবে স্লোগানটি, দল-মত নির্বিশেষে।
আমি বিশ্বাস করি— ‘বঙ্গবন্ধু’ এবং ‘জয় বাঙলা’— এ দুটো অসামান্য দর্শন এখনো বাঙালিকে রাজনৈতিকভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে, নতুবা নেমেসিসবৃত্তে বাঙালির প্রাণত্যাগ অসম্ভব কিছু না।